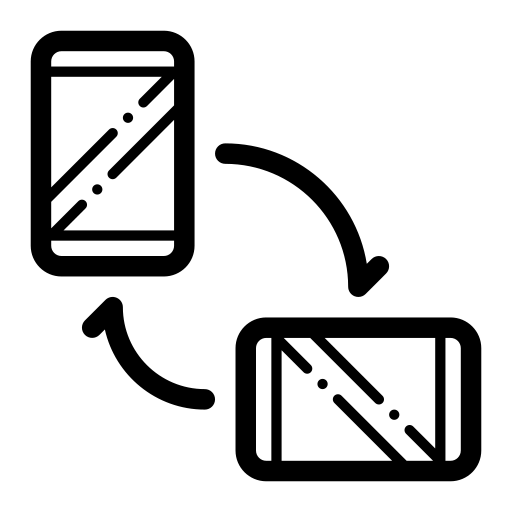 আপনার মুঠোফোনটি ল্যান্ডস্কেপে রাখুন।
আপনার মুঠোফোনটি ল্যান্ডস্কেপে রাখুন।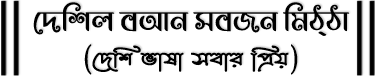
গদ্য ও পদ্য সংকলন
গদ্য ও পদ্য সংকলন
(ক) বঙ্গভাষা - মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১.০ উদ্দেশ্য
১.১ ভূমিকা
১.২ কবিতা
১.৩ সারাংশ ও বিশ্লষণ
(খ) বিপদে মোরে রক্ষা করো - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১.০ উদ্দেশ্য
১.১ ভূমিকা
১.২ কবিতা
১.৩ সারাংশ ও বিশ্লষণ
(গ) কান্ডারী হুঁশিয়ার - কাজি নজরুল ইসলাম
১.০ উদ্দেশ্য
১.১ ভূমিকা
১.২ কবিতা
১.৩ সারাংশ ও বিশ্লষণ
প্রস্তাবনা
ইতিপূর্বে প্রথম ষান্মাসিকের প্রথম গ্রন্থে আমরা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কাব্য নিদর্শন, মধ্যযুগ হয়ে প্রগাধুনিক পর্বের কবিতার একটা পরিচিতি তুলে ধরেছি। চর্যাপদর মধ্যে যে আধুনিক বাংলার বীজ নিহিত আছে এর পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। বৈষ্ণব পদবলী থেকে পাঁচালী এবং কবিয়ালদের রচনাকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়াসও ছিল ওই অধ্যায়ে।
বর্তমান পর্বে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার উন্মেষ লগ্নের অন্যতম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে কাজি নজরুল ইসলাম পর্যন্ত আমাদের পরিসর।
ভারতবর্ষ সহ সারা বিশ্বে মাতৃভাষাবিহীনতার প্রবণতার মুহূর্তে মধুসূদনের ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটির মধ্যে একটি সর্বজনীন আবেদন রয়েছে। বাংলাভাষা এর সৃজন উৎসে থাকলেও এর মধ্যে বিশ্বায়নের জাঁতাকলে পিষ্ট অপরাপর ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ভাষার হাহাকারও প্রচ্ছন্ন।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি অনুপম প্রার্থনাগীতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের সঙ্গে মানব মনের প্রবল শক্তির কথাও ঘোষিত হয়েছে যা কবিতাটিকে একটি উচ্চস্তরের সাধনতত্ত্বের বার্তাবাহী করে তুলেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন যে ‘ভয়শূন্য চিত্ত’র কথা উচ্চারিত হয়েছে কবিকণ্ঠে, সাম্প্রতিককালীন ধর্মাচারের মধ্যে কোথায় যেন সেই মুক্তির বার্তাটি অনুচ্চারিত। ‘বিপদে মোরে রক্ষা করো’ কোনও দুর্বল প্রার্থনা নয়, ভয়শূন্য চিত্তে বিপদের মোকাবিলা করার প্রত্যয় ধ্বনিত হওয়া কবিতাটি সম্ভবত এ সময়ের মুক্তির নিশানা। তা'ই কবিতাটির প্রাসঙ্গিকতা।
আর ধর্মীয় হানাহানি, অসহিষ্ণুতার বিস্তার, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে যখন নিখিল বিশ্ব ক্রন্দনময়, তখন নজরুল ইসলামের ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন’-এ উচ্চারণ কেবল ভারতীয় উপমহাদেশ নয় সারা পৃথিবীর শান্তিকামী জনতারই বাণী হয়ে ওঠে। নজরুলের এ কবিতাটির সংযোজন তাই অপরিহার্য।
কবিতাটি পড়ে আপনি-
- নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ উপলব্ধি করতে পারবেন।
- নিজ দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কবির ঘরে ফেরার একটি মর্মস্পর্শী অন্তরঙ্গ বিবরণ পাবেন।
- সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার আঙ্গিক এবং বিষয় উপস্থাপনার পদ্ধতি ও শিল্পশৈলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩): সাত বছর বয়সে জন্মস্থান যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতায় পড়াশুনার জন্য চলে আসেন এবং একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে খ্যাতি লাভের মোহে তিনি বিলেত যাবার প্রয়াসী হন, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে প্রথমে মাদ্রাজে প্রবাসজীবন শুরু করেন। পিতার মৃত্যুর পর কলকাতায় ফিরে এসে লেখালেখি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। নাটক, কবিতা, অনুবাদকর্ম, পত্রিকা সম্পাদনা, কাব্য রচনা করেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তবে বিদেশি স্বপ্ন, বিদেশি ভাষা-সাহিত্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিলেতে। আইন অধ্যয়ন এবং সাহিত্য পাঠে মনোবিবেশ করলেও নিদারুণ অর্থকষ্ট এবং আশাভঙ্গে দিন কাটাতে হচ্ছিল কবিকে। এ প্রবাসজীবনই তাঁকে ভিন্নতর একটি উপলব্ধির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এরকম এক মুহূর্তে তিনি রচনা করলেন ইউরোপীয় আঙ্গিকে সনেট, অর্থাৎ চতুর্দশপদী কবিতা। এখানেই তাঁর ঘরে ফেরার কাতরতা, হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমি, ফেলে আসা দেশ, ভুলে যেতে চাওয়া মাতৃভাষায় ফিরে আসার বার্তা নিহিত। ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাকে এ পর্যায়ে একটি অন্তরঙ্গ আত্মজীবনীমূলক আখ্যানও বলা চলে।
কবির নামের সঙ্গে জুড়ে থাকা ‘মাইকেল’ অভিধাটি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সূত্রে প্রাপ্ত। অকাল প্রয়াতা পত্নী রেবেকা এবং দ্বিতীয়া হেনরিয়েটা এ দুই সহধর্মিনী কবির জীবনের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতর সঙ্গে জড়িত। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন এবং বিস্তৃত সৃজনকর্ম জীবিতকালেই তাঁকে কিংবদন্তী বানিয়ে দিয়েছিল। কবি যতদূরেই যেতে চেয়েছেন ততই মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা তাঁকে টেনে নিয়েছে একেবারে নিজের প্রাণের কাছে। নিজ পিতৃপরিচয়, কবতক্ষ (কপোতাক্ষ) নদীর তীরে তাঁর সেই জন্মস্থান এবং আপামর বঙ্গবাসী যে তাঁর কত প্রিয় এটা তাঁর স্বরচিত প্রয়াণলিপিতে (Epitaph) প্রচ্ছন্ন রয়েছে যার দিকে বাঙালিকে একবার না একবার তাকাতেই হবে :
দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন!
যশোরে সাগড়দাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;-
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে-
“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!”
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥
খ্যাতির মোহে ঘরছাড়া কবির আত্মোপলব্ধি এবং ঘরে ফিরে আসার আকুতি নিয়েই এ কবিতা। বঙ্গভূমি থেকে বহু দূরে, বঙ্গভাষা থেকে আরো বহু যোজন দূরে প্রবাসে দৈবের বশে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত, শ্রান্ত কবি উপলব্ধি করলেন তাঁর এ নিষ্ফল প্রয়াস পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য। বিদেশি ভাষায় কঠোর কাব্যসাধনা মাতৃভাষা হারা কবিকে ভেতরে বাইরে রিক্ত করে তুলছিল। তিনি ভুলতে বসেছিলেন যে জন্মসূত্রেই তিনি মূল্যবান সম্পদে সম্পদবান। তাঁর মাতৃভাষায় রয়েছে রতনের রাজি, কেন বিদেশি ভাষার দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করবেন। সুদূর ইতালিতে, তাঁর পরম আরাধ্য কবি পেত্রার্কের (১৩০৪-১৩৭৪) ভূমিতে দাঁড়িয়ে পেত্রার্কীয় কাব্যরীতিতে রচিত এ সনেট মাইকেল মধুসূদন দত্তর নতুন জয়যাত্রা সুচিত করল। কবির প্রাণের গভীরে নবজন্ম লাভ করল নতুন বাংলা ভাষা। এ পর্বের একশো দুইটি চতুর্দশপদী কবিতায় মূর্ত হল বঙ্গভূমির নিসর্গ, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, আর কপোতাক্ষ তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রাম। বাংলা ভাষার প্রকাশ সম্ভাবনা উন্মোচিত হল নতুন উজ্জীবনী মন্ত্রে।
মাত্র চৌদ্দটি পঙক্তির কবিতার আঁটোসাটো বাঁধুনিতে প্রকাশিত এ নতুন কাব্য ইস্তেহার। প্রথম আট পঙক্তিতে একটি প্রস্তাবনা এবং শেষ ছ'টিতে সিদ্ধান্ত। এ যেন সুবিন্যস্ত সূচনা-মধ্যমা-সমাপ্তি নিয়ে একটি ধ্রুপদী নাটক। একেবারে মাপাজোখা শব্দে বিশাল একটি বিষয়ের সংস্থান। এখানে আছে একটি আত্মজৈবনিক কাহিনির আদল, ঘটনার টানাপোড়েন, এবং একটা ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এবং এরপর একটি অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স বা ডিন্যুমেন্ট (denoument)। এ ধরনের কবিতার আঙ্গিকই এর ব্যপ্তি, গভীরতা, পরিধি নির্ধারণ করে। পরিমিতিমাত্রায় সামান্য নড়চড় হলেই প্রয়াস ব্যর্থ। ধ্রুপদী কাঠামোয় লিরিক্যাল প্রকাশ কবিতাটিতে দান করেছে বিশিষ্টতা। গভীর অর্ন্তদ্বন্দু এবং যন্ত্রণার অধ্যায় পেরিয়ে প্রত্যয়ের ভূমিতে উত্তরণ এ কবিতায় বর্তমানের মাতৃভাষাবিহীনতা প্রবণতায় একটি নতুন বার্তা এনেছে যা সাম্প্রতিক কালের পাঠকের কাছে কবিতাটিকে নতুন প্রাসঙ্গিকতায় উপস্থাপন করে। কেবলমাত্র বঙ্গভাষী নয়, ভাষার পীড়নে আক্রান্ত ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বের ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং লুপ্তপ্রায় ভাষা ও ভাষিকগোষ্ঠীর কাছেও এর প্রাসঙ্গিকতা।
ভাষা, বিশেষ করে মাতৃভাষা বিষয়ক কবিতার ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন কিছু নয়। মধ্যযুগে পদকর্তা আব্দুল হেকিম (১৬২০-১৬৯০) লিখেছিলেন :-
আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ
দেশি ভাষে বুঝিয়ে ললাটে পুরে ভাগ।।
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত।
যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত।
এ পঙক্তির মধ্যে মাতৃভাষা বনাম আরবি-ফারসির একটা দ্বন্দ্বের আভাস প্রচ্ছন্ন। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ, ধর্মীয় সংস্কার একটা সময় দেশি ভাষা চর্চার অন্তরায় ছিল। মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ সম্বল করে কবি ওই সংকট অতিক্রম করেছিলেন। পরবর্তী পঙক্তিগুলো খুব প্রসাঙ্গিক:
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আল্লা নিরঞ্জন।।
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশ বাক্য কিবা যত ইতি বাণী।।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের কারণ।।
যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশে না যায়।।
মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
মাইকেলের কবিতার প্রায় দুশো বছর আগেকার এ কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে। দুটো কবিতার উদ্দীষ্ট অবশ্য ভিন্ন। মাইকেল সম্বোধন নিজেকে, আব্দুল হেকিম বাক্যগুলো বলছেন সেই সব সংস্কারাচ্ছন্নদের যাঁরা বিশ্বাস করতেন শাস্ত্রকথা বাংলায় লিখলে ‘রৌরব নরকং ভবেৎ’ অর্থাৎ, অনন্ত নরক বাস নিশ্চিত।
বাংলা ভাষার বন্দনা গান গেয়েছেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন, ‘মোদের গরব আশা, আ মরি বাংলাভাষা’। এখানে অবশ্য কোন দ্বন্দু নেই, সংঘাত নেই, আছে ভাষার প্রতি গভীর মুগ্ধবোধ, ভাষার গৌরবে গৌরাবান্বিত হওয়ার উচ্ছ্বাস। আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মুহূর্তে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উচ্চারণ একটি জাতিকে টেনে এনেছিল মহাসংগ্রামে, যে সংগ্রাম গীতটি রচনার অর্ধশতবর্ষ পর জন্ম দিয়েছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের জাতীয়সংগীত হিসেবে মান্যতা লাভ করছে গানটি ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’।
সাম্প্রতিক কালে যখন ভাষার পীড়নে আক্রান্ত ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী —তখন এরই বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শোনা গেল নাগরিক কবিয়ালের উচ্চারণে—
আমি নাগরিক কবিয়াল গেয়ে যাই
প্রতিরোধ তোলা আমার বাংলা গান।।
বাংলাভাষার কসম যখন খাই
শহিদেরা দেন আমার রক্তে টান।
‘একটি’ ভাষার আধিপত্যকে অস্বীকার করে সর্বজনগ্রাহ্য একটি প্রস্তাবনা উঠে আসে কবীর সুমনের এ পঙক্তিতে:
প্রতিটি ভাষাই জাতীয় ভাষার দাবি
কেউ কারো চেয়ে কম নয় বেশি নয়
তবু আমার স্বপ্নলোকের চাবি
বাংলায় পাই পৃথিবীর পরিচয়।
(সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান, কলকাতা, ২০০৩)
এখানে উল্লেখিত তিন ধারার কবিতার বিষয়বস্তু একই, কিন্তু আঙ্গিক, মেজাজ এব প্রকাশভঙ্গি আলাদা। তিন ধরনের কবিতায় তিনটি যুগের চরিত্রলক্ষণ সুস্পষ্ট, যুগের সামাজির রাজনৈতিক প্রচ্ছায়াও এতে প্রকাশিত।
সনেট: ল্যাটিন Soneta শব্দ থেকে উদ্ভুত। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে এ আঙ্গিকের আত্মপ্রকাশ। এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডে এ কবিতা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলায় মাইকেল মধুসুদন দত্ত এর সার্থক রূপকার। চৌদ্দ পঙক্তির এ কবিতার ৮+৬, এ দুই বিভাগ- octave, sestet। এ কবিতার এক একটি চরণে আবার ১৪টি করে বর্ণ। বর্ণ এবং পঙক্তি বিন্যাসের এত কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও সনেটের প্রকাশ সম্ভাবনা, সৃজন সম্ভাবনা এবং শিল্পশৈলী অসীম সম্ভাবনাময়। পেত্রার্ক থেকে শেক্সপিয়ার, মাইকেল থেকে রবীন্দ্র-জীবনানন্দ হয়ে বুদ্ধদেব বসু-সমর সেন-বিষ্ণু দে থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত কবিরা এ আঙ্গিকে লিখে গেছেন। বাংলায় এ কবিতা চতুর্দশপদী কবিতা হিসেবে পরিচিত।
- অনিদ্রায়, নিরাহারে সপি ———
- মজিনু বিফল তপে ——— বরি
- পরদেশে ——— কুক্ষণে আচরি
- এ ——— দশা তবে কেন তোর আজি।
- করিনু
- আচরি
- কেলিনু
- কাটাইনু
- কয়ে দিলা
- কবি কা’কে অবহেলা করেছিলেন?
- পরধন বলতে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে?
- পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কীসের জন্য?
- কবি স্বপ্নে কা’র আদেশ পেয়েছেন?
- কুললক্ষ্মী কী আদেশ করেছেন?
- কবিতাটি কা’কে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে?
- কবি কী উপলব্ধি করেছেন?
- মাতৃভাষার সৃজনসম্ভাবনাকে কবি কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
- এখানে ‘ঘরে ফেরা’র বিশেষ অর্থ আছে কি?
- কবিতাটির সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের সমাজ বাস্তবতার কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে কি, এবং কী ভাবে?
কবিতাটি পড়ে আপনি-
- একেবারে ভিন্নধর্মী একটি প্রার্থনাকাব্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- অলঙ্কার বর্জিত, একেবারে আটপৌরে কথনভঙ্গিতে গভীর ভাবপ্রকাশের শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- আত্মশক্তির অসীম ক্ষমতার স্বরূপ উপলব্ধি করবেন।
- ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি এবং মনুষ্যত্বের প্রতিও আস্থাশীল হবেন।
- কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘গীতাঞ্জলি’র সঙ্গে পরিচিত হবেন।।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম : ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ - ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ: জোড়াসাঁকো, কলকাতা) পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, শিক্ষাবিদ, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছেই তাঁর শিক্ষাগ্রহণ। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত গেলেও এটা অসম্পূর্ণ। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় লেখালেখি শুরু। নিজ বাড়ির অনুষ্ঠানে স্বরচিত গান, নাটক পরিবেশিত হত তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের সামনে। কবি প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, পঠিত নিবন্ধ, পাঠ্যপুস্তক, প্রকাশিত গ্রন্থ, উপস্থাপিত নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, এবং মঞ্চনাট্য - এসব নিয়ে তাঁর বিপুল রচনাসম্ভার। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবির সংগীতসৃজনের অন্যতম উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ওই সময়ে রচিত ‘আমার সোনার বাংলা’ (১৯০৫) গানটি বাংলাদেশ, এবং ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ রচনা (১৯১১) ভারতবর্ষের জাতীয়সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়।
কবি দ্বিতীয়বারের জন্য ইংল্যান্ড যান ১৯১২ সালে, এবং তৎকালীন বিদ্বৎজন রোদেনস্টাইন, ইয়েটস, এজরা পাউন্ড ও অন্যান্যদের সামনে ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুদিত কবিতাগুলো উপস্থাপিত হয়। এই প্রথম পাশ্চাত্যের কাব্যজগতে ভিন্ন ভাষার সুর ধ্বনিত হল, মানুষ এ নতুন উচ্চারণে বিমোহিত হল। মূল গীতাঞ্জলির নির্বাচিত কিছু বাংলা কবিতা এবং সে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত কবিতা নিয়ে নব কলেবরে ইংরেজি গীতাঞ্জলি, Song Offerings প্রকাশিত হল ১৯১২ সালে, এবং এর পরের বছর ১৯১৩ সালে রোদেনস্টাইনের একটি চিত্রসহ ম্যাকমিলান কোম্পানি প্রকাশ করল কবির গ্রন্থটির আরেকটি সংস্করণ যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিলেন ডবলিউ বি ইয়েট্স। বইটি নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয় ওই বছরই। এরপরই ইউরোপে বিভিন্ন ভাষায় কবিগুরুর কবিতার অনুবাদ শুরু হয়।
১৯১৬ সালে কবি জাপান ইংল্যান্ড, ফ্রানস এবং আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ করেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখেন। এবারের ভ্রমণে কবি বিংশ শতাব্দীর আত্মিক সংকট, বিশ্বব্যাপী উগ্রজাতীয়তাবাদের আগ্রাসন, আধিপত্যবাদের স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর সাহিত্য জীবনে সূচিত হল নতুন অধ্যায়।
১৯১৮ থেকে কবি শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্রতী হিসেবে মনোনিবেশ করলেন। দুই বছর পর বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। কবির স্বপ্ন ছিল ‘শান্তিনিকেতন’ বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে, ওখানে সর্বজাতির মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে, সংকীর্ণতার যুগের অবসানে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর নামের সঙ্গে বিশ্বকবি তকমাটি কেন সুপ্রযুক্ত তা ওই স্বপ্নের মধ্যেই নিহিত।
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি সরকার প্রদত্ত ‘নাইট’ উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯২৬ সালে কবি ইতালি ভ্রমণকালে রঁমা রোল্যার সান্নিধ্য লাভ করেন। রোল্যা তাঁকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন।
বিশ্বপর্যটক কবি সারা জীবন ৮২টি দেশ ভ্রমণ করেন, এর মধ্যে ইউরোপ আমেরিকা ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোও রয়েছে। তাঁর সাক্ষৎ হয় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গেও; কবির ভ্রমণ তালিকায় চিন (১৯২৪) এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়াও (১৯৩০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিগুরু ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতা, ‘The Religion of Man’ এর মাধ্যমে ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মভাবনাকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন যেখানে বাংলার বাউল, সুফি সাধনতত্ত্ব, লোকায়ত ধর্মাচার, সহজিয়া তত্ত্ব বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
আসাম, ত্রিপুরার সঙ্গে ছিল কবিগুরুর বিশেষ আত্মিক সম্পর্ক। তৎকালীন বিশিষ্ট অসমিয়া বিদ্বৎজন কবিসান্নিধ্য লাভ করেন, গৌহাটি, শিলঙে কবি একাধিকবার সংবর্ধিত হন, আতিথ্য গ্রহণ করেন। শিলঙে বসবাস কালে কবি তাঁর অন্যতম সাহিত্যকর্মগুলোও রচনা করেন, শৈলশহরের প্রেক্ষাপটে কবি রচনা করেন একটি উপন্যাসও (শেষের কবিতা)। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে কবি আসাম-বেঙ্গল রেল চড়ে পাহাড় লাইনে লামডিং-বদরপুর-করিমগঞ্জ হয়ে সিলেট যাবার পথে করিমগঞ্জ রেলস্টেশনে সংবর্ধিত হন। সিলেট ভ্রমণকালে ওখানকার সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য এবং মণিপুরি শিল্প এবং নৃত্যকলার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। এ অঞ্চলের স্থান নাম, নিসর্গ, ফুল, ফল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিও তাঁর সৃজনকর্মে স্থান পায়। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে কবির গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং নানাবিধ কর্মকাণ্ডে রাজসভার আনুকূল্যও তিনি লাভ করেন। কবি ত্রিপুরা রাজসভার প্রেক্ষাপটে রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস ‘রাজর্ষি’ এবং নাটক ‘বিসর্জন’, মণিপুরের চিত্রাঙ্গদাও স্থান পান তাঁর বিশিষ্ট নৃত্যনাটিকায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা এবং কর্ম যেমন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও বিশাল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি তাঁর সৃজনশীলতায় বিশেষ বৈচিত্র্য আসে, আধুনিক প্রেক্ষিতে তাঁর সৃষ্টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকে। কবিতা, গানের ভাষা, প্রকাশভঙ্গিতে যেমন নতুন প্রাসঙ্গিকতার উদ্ভাসন ঘটেছে, তেমনি চিত্রকলা, গদ্যরীতিতেও যুগের অভিঘাত দিয়েছে। নতুন মাত্রা। ১৯৪১ সালে মৃত্যুর তিনমাস আগে কবি রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তৎকালীন বিশ্বময় সংকটের স্বরূপটি প্রকাশিত।
এর পনেরো বছর পূর্বে ২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (৫ মার্চ, ১৯২৭) কবি ৬৫ বছর বয়সে লিখেছিলেন একটি গান যেখানে ওই ‘ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয়’-এর হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে-
‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ’।
দেশবরণ্য নেতৃবৃন্দ-মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ ছাড়াও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, কাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।
তাঁর টানে দেশবিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতনে আসেন। এদের মধ্যে চার্লস অ্যানড্রুজ, সিলঁভ্যা লেভি, গুইসেপে তুচ্চি এরা প্রধান। শান্তিনিকেতনের চিনাভবন বিশেষ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে কবির প্রয়াসে। তৎকালীন ভারতের বিশিষ্ট শিল্পী নন্দলাল বসু, রামকিংকর বেইজ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সংগীতজ্ঞ ভীমরাও শাস্ত্রী, শাস্তিদের ঘোষ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ প্রশান্ত মহালনবিশ, সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশি, সৈয়দ মুজতবা আলী এরা শান্তিনিকেতন আলো করে ছিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম, বরোদার সায়জি ছাড়াও ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সঙ্গে কবির বিশেষ সখ্য ছিল।
ব্যক্তিগত জীবনে কবি একেবারে শৈশব থেকে মৃত্যুর আগের বছর পর্যন্ত অনেক প্রিয়জন বিয়োগ দেখে গেছেন – এরমধ্যে ভ্রাতৃবধূ কাদম্বরী দেবী, নিজ পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, নাতি ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রাণপ্রিয় বন্ধুরাও আছেন। এত যন্ত্রণা সত্বেও কবি জীবনে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। ‘বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই, নেই’, ‘পথের শেষ কোথায়’ এসব প্রশ্ন তাঁকে পীড়িত করলেও কবি স্থির ছিলেন এ প্রত্যয়ে: ‘মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়’।
বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।
ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা বিপদে রক্ষা করার কাতর নিবেদন নয়, দুঃখ থেকে ত্রাণ বা ভারমুক্তিও নয়, বিপদে মনোবল অটুট রাখা, দুঃখতাপ সইবার শক্তি, সাহস ও মনোবল কামনা করে এ আন্তরিক নিবেদন। অসহায়ের আত্মসমর্পন নয়, কোনও আকুল, করুণ কাতর বিনয়ও নয় এ এক অভিনব উচ্চারণ। কবিতাটিতে ঈশ্বরকে তুচ্ছ জাগতিক দুঃখকষ্টের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখাও নয়, সমস্ত জাগতিক চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে উঠে ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং আস্থার প্রকাশই এখানে উচ্চারিত। ঈশ্বরভক্তি মানে যে নিজের উপর আস্থা হারানো নয় এটাই এ কবিতায় প্রকাশিত। ঈশ্বরপ্রেম মানুষকে নিশ্চেষ্ট করতে পারে না, ঈশ্বরপ্রেমই মানুষকে বিপদে অকুতোভয় করতে পারে, এটাই কবির বিশ্বাস।
এ অভিনব উচ্চারণ আমাদের চমকিত করে বই কি। পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে অধ্যাত্মিক প্রার্থনা ও সংগীতে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণেরই সুর। কিন্তু এ কবিতায় একেবারে ভিন্ন সুর ধ্বনিত। ঈশ্বর মহান, সর্বশক্তিমান, কিন্তু মানুষও যে অসীম শক্তিধর তা’ও কবির বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা সম্ভব। অপর একটি কবিতায়ও কবি বলছেন- ‘নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো’; তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, 'নিজেরে পরে করিতে ভয় না রেখো সংশয়' (১৯৩০)। (তখন কবির বয়স ৬৮ বৎসর)। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের ‘মেটাফিজিক্যাল কবি’, বিশেষ করে জন ডানের কিছু কবিতায় এ ধরনের উচ্চারণ শোনা যায়। Holy Sonnet, Hymn to God my Father এবং অনুরূপ কবিতায় দেখা গেছে কবি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে মত্ত, কখনও ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, কখনও বা আদেশ, আবার কখনও কবি ঈশ্বরের কাছে নতজানু। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ওই বৌদ্ধিক কূট যুক্তিজাল নেই, কিন্তু যা আছে তা একেবারে অভিনব, আধুনিক। চল্লিশ বছর বয়সে কবির এ আত্মোপলব্ধি তাঁকে পরবর্তী দিনগুলোতে আরও গভীর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন ৩৮ বছর বয়সেও কবির প্রার্থনা-
‘প্রভু মোচন কর ভয়
সব দৈন্য করহ লয়
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত কর নিঃসংশয়’ (১৯০৬)।
‘গীতাঞ্জলি’র কবিতা রচনার প্রেক্ষিত নিয়ে কবি বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনের মুক্ত আবহাওয়ায় যেখানে ‘মানবশিশুদের জন্য মুক্তি ও আনন্দের দ্বার অবারিত’ করে দেওয়া ছিল লক্ষ্য, যেখানে ‘শিশুদের প্রাণশক্তি আর উচ্ছ্বাস, তাদের কলকণ্ঠ আর কলতান চারদিকের আবহাওয়াকে আনন্দরসে ভরিয়ে দিত আর আমি তা আকণ্ঠ পান করতাম।... ওই আবহাওয়ায়, ওই পরিবেশে, আমি ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতাগুলো লিখেছি। মধ্যরাতে উজ্জ্বল তারকাখচিত ভারতীয় আকাশের নিচে বসে আপনমনে আমি গানগুলি গাইতাম। আর প্রত্যহ প্রত্যুষে এবং গোধূলিবেলায় অন্তরবির রশ্মির আভায় এইসব কবিতা লেখা আমার চলছিল যতদিন না বৃহত্তর জগতের কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাগিদটা আবার নতুন করে অদম্য হয়ে উঠল।' ১৯২১ সালে, ২৬ মে স্টকহোমে সুইডিস আকাদেমিতে বক্তৃতায় কবির স্বীকারোক্তি, 'এখন বুঝতে পারি যে এইসব আনন্দমুখর শিশুদের সান্নিধ্যে, দেশের মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে, বিচ্ছিন্নতার যে জীবন আমি বরণ করে নিয়েছিলাম, তা থেকে বেরিয়ে আসাটা ছিল বৃহত্তর জগতে আমার তীর্থযাত্রার সূচনামাত্র'।।
(অনুবাদ সুজিৎ চৌধুরী, 'গীতাঞ্জলি, নোবেল পুরস্কার বিতর্ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', করিমগঞ্জ, ২০১৭)
পাঠ্য কবিতাসহ সার্বিকভাবে গীতাঞ্জলির প্রার্থনামূলক কবিতাগুলো যে নিশ্চেতনার নয়, উজ্জীবনের, নীরব, একক সাধনার নয় সমবেতভাবে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ার প্রস্তুতি, কবিতাটিকে এ প্রেক্ষাপটে পাঠ করলে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।
‘বিপদে মোরে রক্ষা করো’
কবিতাটি বাংলা 'গীতাঞ্জলি' বইতে সংকলিত হলেও (৪ নং) ১০৩টি কবিতা সম্বলিত ইংরেজি ভার্সনে নেই।
কবিতার রচনাকাল: ১৩১৩ বঙ্গাব্দ (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)
ওই বছর ২৩ নভেম্বর কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ২৭ জুলাই, ১৯৪১ তারিখ মুখে মুখে শেষ কবিতা ‘প্রথম দিনের সূর্য’-র শ্রুতিলেখন দেবার পর কবি এ কবিতাটি শুনতে চান। রাণী চন্দ, অনিল চন্দ (কবির সচিব) স্মৃতি থেকে পুরো শোনাতে না পারায় ‘গীতাঞ্জলি’ এনে পাঠ করা হল। কবি বলেন বইটি করে রেখে দিস্- এগুলো মন্ত্রের মতন।
-শঙ্খ ঘোষ, দামিনীর গান, প্যাপিরাস, ১৪০৯
‘গীতাঞ্জলি’ প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনা রয়েছে এ পাঠক্রমের ‘প্রথম ষান্মাসিক, ১ম পত্র’ বইতে (পৃ. ৪৬-৪৯)
- বিপদে রক্ষা নয়- কবির প্রার্থনাটা কী?
- দুঃখের মুহূর্তে সান্ত্বনার পরিবর্তে কবি কী প্রার্থনা করেছেন?
- সংসারে ক্ষতি, বঞ্চনা পেলেও কবি কী চেয়েছেন?
- ত্রাণের পরিবর্তে কবি কী প্রার্থনা করেন?
- জীবনের ভার লাঘব করার পরিবর্তে কবি কী চেয়েছেন ?
- কবির সর্বশেষে প্রার্থনাটা কী?
- ‘তোমারে যেন না করি সংশয়’ — কার কথা বলা হয়েছে?
- ‘বহিতে পারি এমনি যেন হয়’ — কী ‘বহিতে পারি’ বলা হয়েছে?
- ‘নম্রশিরে সুখের দিনে’ — কী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কবি?
- ‘নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়’ — কোন অবস্থায় এ প্রার্থনা করা হয়েছে?
কবিতাটি পড়ে আপনি-
- পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সামনে যে-প্রত্যহ্বান এসেছিল এর একটি ধারণা পাবেন
- জাতীয় সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যভাবনার সূত্রগুলো সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- কবির ইতিহাসচেতনা, রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তাবোধর পরিচয় পাবেন।
- বর্তমান প্রেক্ষিতে কবিতাটির গভীর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।
কাজি নজরুল ইসলাম (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ - ১১ই ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ): জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতা কাজি ফকির আহমদ, মাতা জাহেদা খাতুন। দশ বছর বয়সে পিতৃহারা কবি গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইতি টানেন। তবে স্বল্পকালীন স্কুলজীবনে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মতো শিক্ষক এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো সহপাঠীর সংস্পর্শে এসে বিশেষ লাভবান হন। চাচা বজলে করিমের কাছে ফারসি পাঠ নিয়ে, হাজি পালোওয়ানের মাজার শরিফে খাদেমগিরি এবং পীরপুরে মসজিদের ইমামের কাজ করেও বিশেষ লাভবান হন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে দশম শ্রেণীর পরীক্ষা না দিয়েই সৈনিক জীবন গ্রহণ করে পশ্চিম ভারত এবং অতঃপর মধ্যপ্রাচ্যে গমন, তিন বছর পর ফিরে এসে কলকাতায় সাহিত্যকর্ম, পত্রিকা সম্পাদনা, স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ। এত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে কাজি নজরুল ইসলামের সৃজনকর্ম ধাবিত হয় বহু বিচিত্র ধারায়। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য 'ধুমকেতু' পত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন তরুণ সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন, এবং এতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লিখে রাজদ্রোহের অভিযোগ অভিযুক্ত হয়ে এগারো মাস কারাবন্দি হন। মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশনে বসলে কবিগুরুর অনুরোধে তা প্রত্যাহার করেন, জেলে বসে অগ্নিগর্ভী কবিতা ও গান লিখে যান এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত হয়ে কবিতা আর গানে বঙ্গভূমিকে উত্তাল করে তোলেন।
নিজ ধর্মবিশ্বাসে স্থিত থেকেই নজরুল ইসলাম কখনও বৈষ্ণব মহাজনী ঐতিহ্যের উত্তরসূরী হিসেবে রচনা করেছেন কীর্তন, রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী, কখনও শাক্ত কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রচনা করছেন শাক্ত পদ। একদিকে তিনি যেন বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস, অপরদিকে তিনি এ যুগের রামপ্রসাদ-কমলাকান্তও। অবশ্য ইসলামীসংগীত রচনায় বঙ্গভূমিতে তাঁর ভূমিকা ভগীরথের। এ ধরনের সৃজনক্ষমতা সারা বিশ্বে আর কোনও কবি দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ইংরেজ কবি শেলির 'Revolt of Islam' (১৮১৮) এ ক্ষেত্রে অবশ্য একটিমাত্র দৃষ্টান্ত।
‘একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য’ নিয়ে কাব্যজগতে যে মহাবিদ্রোহীর আত্মপ্রকাশ, তিনি একদিকে অপূর্ব মেলোডিয়াস প্রকৃতিবন্দনা এবং প্রেমসংগীত রচনা করছেন, অপরদিকে গাইছেন, 'কারার ওই লৌহ কবাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'..., গাইছেন 'লাথি মার ভাঙ রে তালা, যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা'। একদিকে যিনি গাইছেন 'আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ / এই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হজরৎ', তিনিই গাইছেন, 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', তিনিই আবার ভক্ত হয়ে কৃষ্ণবিরহে গাইছেন, 'ওরে নীল যমুনার জল, বল রে মোরে বল, কোথায় ঘনশ্যাম, আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম'।
কাজি নজরুল ইসলাম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিয়ে করেন। কনিষ্ঠপুত্র বুলবুলের অকালপ্রয়াণে কবি গভীর আঘাত পান। শাশুড়ি গিরিজাবালা দেবীকে কবি নিজপুত্রের মতোই সেবাযত্ন করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রী পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যান, এবং কবির নিজের জীবনেও নানা ধরনের সমস্যা এসে তাঁকে জর্জরিত করে তোলে। ১৯৪২ সালে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নির্বাক হয়ে যান। ইউরোপে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করলেও কবিকে আর সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে ওই দেশে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং ওখানেই তিনি ১৯৭৬ সালে প্রয়াত হন।
‘অগ্নিবীণা’ (১৯২২), ‘দোলনচাঁপা’ (১৯২৩), ‘ছায়ানট’ (১৯২৪), ‘বুলবুল’ (১৯২৮) ‘নজরুল-গীতিকা’ (১৯৩০)-সংকলনগুলি কবির বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাছাড়া ‘সঞ্চিতা’ (১৯২৮) গ্রন্থটি অদ্যাবধি কবির জনপ্রিয় কাব্যসংকলনের অন্যতম। মহাবিদ্রোহী এ করি প্রাসঙ্গিকতা যে কখনও ফুরাবে না তা তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র কয়েকটি পঙক্তির মধ্যেই প্রকাশিত। যতদিন পৃথিবীতে অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় থাকবে কবির প্রতিবানে ভাষাও মানুষকে উজ্জীবিত করবে। তিনি ঘোষণা করেন —
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হবো শান্ত।
দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরন
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পন।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র
গিরি সংকট, ভীরু যাত্রীরা গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কান্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চলো টানি, নিয়াছ যে মহাভার!
কান্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পূনর্বার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কান্ডারী হুশিয়ার!
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ঘনীভূত সংকটের প্রতিকারকল্পে রচিত এ কবিতা আজ জাতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ এবং একটি ঐতিহাসিক সংগীত। নজরুল ইসলামের কণ্ঠে এ গানটি শুনে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন- "বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয়সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।" প্রাক্-স্বাধীন বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মিছিলে, ময়দানে, সভাসমিতিতে, সংগ্রামে, প্রতিরোধে বার বার এ কবিতা উচ্চারিত হয়েছে, সুরে উচ্চারিত এ গানটি গীত হয়েছে সমবেত কণ্ঠে। কবিতাটির আবেদন এত গভীর যে আজও যে-কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, এমনকি যেখানে কোনও সংগ্রাম বা প্রতিবাদের অনুষঙ্গই নেই সেখানেও শ্রোতারা এ গান কিংবা আবৃত্তি শুনতে চান আগ্রহ ভরে।
পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বানই এ কবিতার মূল। যে ঐক্যের বন্ধন শিথিল করা প্রতিপক্ষের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, এদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে কবির এ আওয়াজে রয়েছে বাঙালির গৌরবজনক ইতিহাসের স্মৃতি, শহিদের আত্মত্যাগের কথা, রয়েছে বাঙালির মুঢ়তার কথাও। জাতীয় জীবনে দুর্যোগ মুহূর্তেই দেশবাসীর মনে জাতিবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সমবেত আন্দোলনকে দিকভ্রষ্ট করতে চায়, কবিতাটিতে এদিকে সাবধানবাণী শোনানো হয়েছে। এ সংগ্রাম যেন তরঙ্গমুখরিত নদীতে একটি নৌযাত্রা যেখানে সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য কবির আহ্বান, যে ব্যাক্তি জাতি-ধর্মের প্রশ্ন ভুলে সব যাত্রীদের নিরাপদ অভীষ্টে পৌঁছে দিতে সক্ষম।
বাঙালির গ্লানিকর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি পলাশীর প্রান্তরের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। যাঁরা ইংরেজদের কারাগারে বন্দি, যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন দেশের জন্য এদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশবাসীর প্রতি কবির এ আহ্বান বিভেদের রাজনীতি দূর করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নেমে যাওয়ার।
কবিতাটি একই সঙ্গে সমসাময়িক এবং সর্বকালীনও। তাৎক্ষণিক বাস্তবতা উঠে এলেও এর মধ্যে একটা যুগোত্তীর্ণ আবেদন রয়েছে। পাঠকরা সহজেই সাম্প্রতিক ভারত কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে এ কবিতাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারেন। দেশপ্রেমের এ কবিতায় আক্ষেপ, বিক্ষোভের সঙ্গে একটা উদ্দীপনার সুরও নিহিত। এক একটি পঙক্তি যেন নাবিকদের দুস্তর পারাবারে যাত্রায় এক একটি সফল উত্তরণ। কবিকৃত সুরারোপ এতে করেছে বিশেষ প্রাণসঞ্চার। স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকগুলোতে ভারতীয় উপমহাদেশের পরিবর্তিত রাষ্ট্রনৈতিক চিত্রটিকে সামনে রাখলে এ কবিতার বিস্তারভূমি তো অবিভক্ত বাংলা সহ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশ তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশই, যেখানে হিন্দু-না ওরা মুসলিম এ বিভেদমূলক তত্ত্বের বিরুদ্ধে মানবিক দর্শন সততই প্রতিষ্ঠা চাইছে।
- কবিতায় কান্ডারী কে?
- যাত্রী বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে?
- দুর্গমগিরি, কান্তার মরু এখানে কীসের ইঙ্গিতবাহী?
- ‘যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা’ বলতে কবি কী বোঝাচ্ছেন?
- পলাশীর প্রান্তরে কী ঘটেছিল?
- কবিতার শেষ চরণে কা’দের বলিদানের কথা বলা হয়েছে?
- “হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন” — কার উদ্দেশে বলা হয়েছে?
- ‘পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে’ — কীসের সন্দেহ জেগেছে?
- ‘ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছ হায়’ — এখানে কোন্ ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে?
- কা’রা ‘জীবনের জয়গান’ গেয়েছেন?
